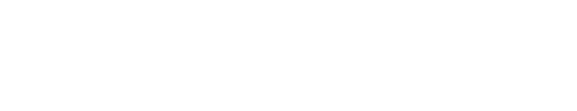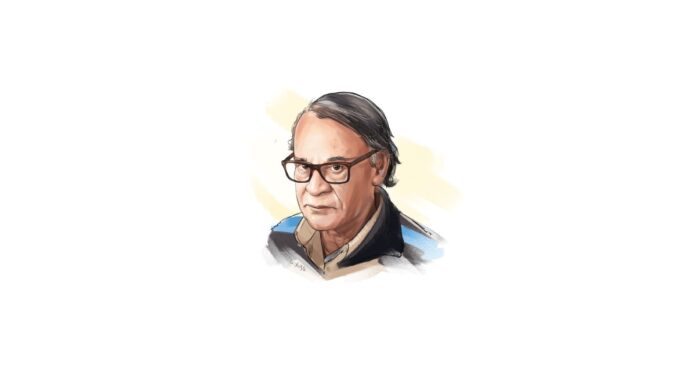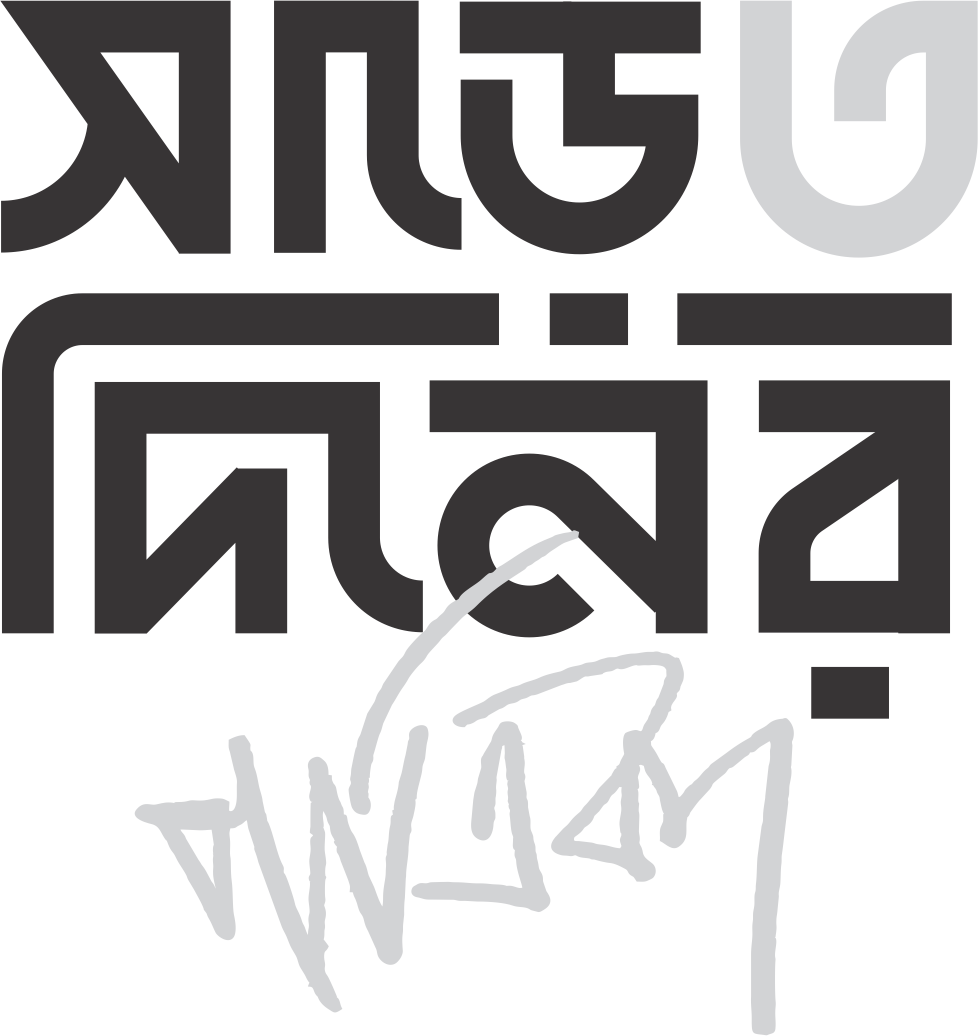- স্যার, আপনি তো দীর্ঘদিন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনকে নিয়ে কাজ করেছেন। জয়নুলকে বেছে নেওয়ার কারণ কী ছিল?
মতলুব আলী : জয়নুলকে বেছে নেওয়ার কারণ ঠিক ভেবে দেখিনি। কীভাবে কাজ করা শুরু করলাম, তা বলা যেতে পারে। তিনি যখন আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন, স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সাল, তখন বাংলাদেশ বেতার থেকে ‘বেতার বাংলা’ নামে একটা পত্রিকা বের হত। পত্রিকার সম্পাদক জয়নুলকে নিয়ে লেখার প্রস্তাব দিলেন। আমি সেখানে লিখলাম। সেটাই ছিল আমার প্রথম জয়নুলকে নিয়ে লেখা। লেখাটা নিয়ে সম্পাদক আমাকে একদিন বললেন, তুমি কী লিখেছ, জানো? যাকে নিয়ে লিখেছ, তিনি আবেদীন; তিনি অমর। আমার বয়স তখন বেশি না। আমি মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খেলাম। আবেদীন অমর হবেন, এই ব্যাপারটা আমাকে প্রভাবিত করল। নিজের লেখা থেকে নিজে প্রভাবিত হলাম। এটা একটা দিক। জয়নুল আবেদীন হচ্ছেন একমাত্র শিল্পী, যিনি মাটিবর্তী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে আর্ট কলেজে পড়াশোনা করতে গেলেন এবং তিনি পরে দেশের মাটিতে এসেছেন। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিল্পচর্চা শুরু করলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলাচর্চা শুরু হলো আধুনিক শিল্পকলাচর্চার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। জয়নুল আবেদীন শুরু থেকেই আলাদা হয়ে যান।
- আপনি তো কাছ থেকে জয়নুলকে দেখেছেন। আপনার দেখা ব্যক্তি ও শিল্পী জয়নুল কেমন ছিলেন?
মতলুব আলী : উনি খুব দিলখোলা একজন মানুষ ছিলেন। যা বলতে চাইতেন, মন থেকে বলতেন। উনি শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। নিজের ছাত্রদের কাছে প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। আমার একজন সিনিয়র ছিলেন, যিনি শিল্পী ছিলেন, নাম ছিল রেজাউল করিম। তার এক্সিবিশনের জন্য জয়নুল স্যারের বাণী নিতে গেলাম, স্যার বললেন, আমার লেখার সময় নাই। আমি বলছি, তোমরা শুনে স্ক্রিপ্ট কর। পরে যখন স্ক্রিপ্ট করে স্যারের কাছে নিয়ে যাই, উনি খুব আপ্লুত হলেন। কাজ শেষে হাসিমুখে বললেন, এবার তোমরা যাও। আমার বিদেশি এক বন্ধু আসবে। স্পষ্টভাষী ছিলেন। যা কিছু বলতেন মন খুলে বলতেন। কোনো ভণিতা ছিল না।
- উনি কি ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন?
মতলুব আলী : হ্যাঁ। আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। উনার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। উনি একটা উপন্যাস লেখা শুরু করেছিলেন। পাণ্ডুলিপি পড়ে দেখেছি, আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ছিল। সেটা আর ছাপা হয়নি।
- জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বে এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পচর্চার শুরু। তিনি যে স্বপ্ন থেকে শুরু করেছিলেন, তা কি বাস্তবায়ন হয়েছে?
মতলুব আলী : সেটার বাস্তবায়ন তো হয়েছে। সেই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর অনেক ছেলেমেয়ে বের হয়। প্রথমে কলেজ ছিল, তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় হলো। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ হিসেবে গ্রহণ করল। এটা একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে, বৈশাখ থেকে শুরু করে মঙ্গল শোভাযাত্রা, লোকচর্চাকে গুরুত্ব দেওয়া, সৃজনশীল শিল্পকলার যে চর্চা, সেখানে সারাদেশে ছড়িয়ে আছে শিল্পীরা। সারাদেশে আর্ট বিষয়ক যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং ছড়িয়ে পড়েছে তার পেছনে জয়নুল আবেদীনের গড়া আদি প্রতিষ্ঠান যুক্ত।
- আপনার একটা লেখায় জানিয়েছিলেন, জয়নুলের অন্তিম সময়টা আপনার স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে। এই ব্যাপারে কিছু বলুন।
মতলুব আলী : ওনাকে শেষবারের মতো পিজি হাসপাতালে নেওয়া হলো। আমি ও আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক শিক্ষক ছিলেন দেলোয়ার হোসেন দেলু, বড় ভাইও ছিলেন। দেলু ভাইসহ প্রায়ই স্যারকে দেখতে যেতাম। উনি যে রুমে ছিলেন আমরা সেই রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। উনি জানালা দিয়ে আমাদের দেখছিলেন। আমরাও দেখছিলাম। উনি ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছেন। শ্বাসের শব্দ হচ্ছিল। শরীরটা আন্দোলিত হচ্ছিল। হঠাৎ একসময় থেমে গেল। তখন দেলু ভাই বললেন, ভালো লাগছে না! চলেন যাই। ওখান থেকে এসে সেই দৃশ্যটা লিখি।
- জয়নুলের নামের পূর্বে শিল্পাচার্য যুক্ত হওয়ার গল্পটা শুনি।
মতলুব আলী : বাংলাদেশের যে চারুকলাচর্চা, তা জয়নুল আবেদীনের নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। উনার লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠানটিকে ভালো মানের করে গড়ে তুলবেন। শুধু ছবি আঁকা শিখবে তা নয়, রুচির বিকাশের মধ্য দিয়ে রুচিশীল শিল্পসমাজ গড়া। সেই প্রতিষ্ঠানটা এমন একটা পর্যায়ে চলে এলো তখুনি, সেই ষাটের দশকে, উনার এই প্রত্যাশার সঙ্গে সবার মত মেলে না। জয়নুল আবেদীনের যে সৃজনশীলতা ও তুখোড় ব্যাক্তিত্ব তাতে অনেকের ইর্ষা ছিল। তিনি তখন প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছেন। আর্ট কলেজকে বলা হত জয়নুল আবেদীনের আর্ট কলেজ। সেই সময় জয়নুল আবেদীন লোকশিল্প বা কারুশিল্প নিয়ে একটা প্রদর্শনী করেছিলেন। অন্যরা আগ্রহ দেখাননি। নিজ প্রতিষ্ঠানে জয়নুল আবেদীন বিরোধিতার শিকার হয়েছিলেন। এইসব মিলে জয়নুল আবেদীনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়। ১৯৬৭ সালে তখন আমি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, হঠাৎ আমরা জানলাম, আবেদীন স্যার ডিপার্টমেন্টে আর আসবেন না। রেজিগনেশন লেটার দিয়েছেন তিনি। আমরা একদিন স্যারের বাসায় গেলাম, অনুরোধ করলাম, স্যার আসতে হবে। তিনি ভীষণরকম একরোখা ছিলেন। তিনি আর আসেননি। তখন আমাদের ছাত্রসংসদ নামে যে কমিটি ছিল, সেই কমিটিতে ছাত্ররা মিলে ঠিক করা হলো, একটি এক্সিবিশন উদ্বোধন করার জন্য স্যারকে আমন্ত্রণ। এবারও স্যারকে রাজি করা গেল না। তখন ঠিক করা হলো উনার নামে এক্সিবিশনটা উদ্বোধন করব। সেই দৃশ্যটা আমার মনে পড়ে, লাল ফিতা বাঁধা আছে, আমার সোনার বাংলা গান গাওয়া হলো, তারপর একটা পরিবেশ তৈরি হলো, আমরা পাঠ করলাম, যে নাম আমাদের ব্রত গ্রহণের প্রেরণা, যার প্রেরণা আমাদের উত্তর জীবনের পাথেয়, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনকে আমরা স্মরণ করছি এই শুভ উদ্বোধনে। সেই থেকে শিল্পাচার্য অভিধাটি শুরু হলো। এর পেছনে পুরোপুরি ছাত্রদের অবদান ছিল।
- নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যাওয়ার পেছনে জয়নুল আবেদীনের যে ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি ছিল, সেটা কি উনি প্রকাশ করেছিলেন?
মতলুব আলী : না, উনি প্রকাশ করেননি। কাউকে বলেননি। উনার জীবনের শেষপর্যায়ে কলেজে হান্নান ভাই বলে একজন পিয়ন ছিলেন, যিনি দেখা করতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তখন তিনি কান্না করে বলেছিলেন, হান্নান আমি আবার যেতে চাই। স্মরণসভায় হান্নান ভাই এই কথা জানান।
- জয়নুল আবেদীনের চেতনাকে ধারণ করে প্রতিবছর জয়নুল মেলার আয়োজন করে চারুকলা অনুষদ। তরুণ প্রজন্মের কাছে জয়নুলের চেতনাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই মেলা কতটুকু যথেষ্ট?
মতলুব আলী : যেহেতু এটার জয়নুল মেলা নাম দেওয়া হয়েছে, শুরু থেকে উনার জন্মদিনে জয়নুল নামটা ধরে লোকশিল্পীদের নিয়ে এসে সমাবেশ করা হত। উনি যে আদর্শ লোকশিল্প গ্রাম করতে চেয়েছিলেন সোনারগাঁওয়ে, সেটা ভেস্তে গেছে। যে সমস্ত কারিগররা ছিল, তারা প্রায় ক্ষয়িষ্ণু, তাদেরকে নতুনভাবে তৈরি করে নতুন জেনারেশন গড়াÑ সেটা ছিল জয়নুল আবেদীনের লক্ষ্য। এখন যেটা হচ্ছে, তা হলো কিছু লোকশিল্পীদের জিনিসপত্র দিয়ে মেলা করা হচ্ছে, তারা অংশগ্রহণ করেন। বেচাকেনা হয়। জয়নুল আবেদীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এরকম ছিল না।
আপনি তো জয়নুলকে নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করছেন, এই দীর্ঘ যাত্রায় তাকে নিয়ে নতুন কোন দিকটি আবিষ্কার করলেন?
মতলুব আলী : নতুন কোনো ধারণা তো আমি সৃষ্টি করব না। আমার টোটাল যে চিন্তাটা, জয়নুলকে যে জায়গাটায় আমি রাখি বা রাখতে চাই, সেখানে একজনের নাম বলতে বললে জয়নুলের নাম বলব। আমরা সবাই উনাকে শিল্পী হিসেবে জানি। আমি তাকে বলি ‘সংস্কারক বুদ্ধিজীবী’। সংস্কারটা এরকম ছিল, যেমন ছবি আঁকতে দেওয়া হবে না, কুসংস্কার ছিল সমাজে। উনার মধ্যে সংস্কারধর্মী প্রবণতা ছিল। কমন যে ধারাটা ছিল তিনি তার মধ্যে যান নাই। খুব কৌশলে এগিয়েছেন তিনি। এছাড়া উনার ছবিতে মৌলিক কনট্রিবিউশন আছে। যখন উনি ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হচ্ছেন কলকাতা আর্ট স্কুলে, তখন ওখানকার শিক্ষকরা চেয়েছিলেন প্রাচ্যকলায় ভর্তি হোক, যেটা ইন্ডিয়ান আর্ট ছিল সেসময়, উনি কিন্তু রাজি হন নাই। ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য ধারায় যে ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং সেখানে তিনি ভর্তি হন। তার ছবির প্রধান বাহন হচ্ছে লাইন বা রেখা। এই রেখা কিন্তু প্রাচ্যকলা শিল্পের সম্পদ। বলা হয়ে থাকে তাঁর হাত হচ্ছে পাশ্চাত্য, চোখ হচ্ছে প্রাচ্য।
- জয়নুল যখন এদেশে শিল্পচর্চার আন্দোলন শুরু করলেন তখন নব্য উপনিবেশিক শাসন। শিল্পচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। আজকের সময়ে শিল্পচর্চার অনুকূল পরিবেশ কি আছে?
মতলুব আলী : সেটা যদি ব্যাপক অর্থে বলি, এটা এক শ্রেণির মধ্যে আছে। যদি ধরি হিন্দু ও মুসলমান কমিউনিটি।তাহলে দেখব হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃতিচর্চাটা ধর্মের মধ্যে রয়েছে। ফলে বাচ্চারা আর্টকালচারের মধ্য দিয়েই বড় হয়। সেখানে সমস্যা নাই। সমস্যা হলো মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে। মুসলিম ধর্মে নিষেধ আছে। শহীদ মিনারে ফুল দিই, একটা শ্রেণি মনে করে আমরা পূজা করি। আসলে তো তা নয়। এরপর আলপনার কথা বলি। আলপনা হচ্ছে একমাত্র লোকশিল্পের ফর্ম, যে ফর্মটা আমাদের নাগরিক জীবনে চলে এসেছে। সেই আলপনাতেও বাঁধা দেওয়া হয় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। এই সমস্যাগুলো রয়েছে এখনো।
- আমাদের শিল্পকর্ম কতটা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পেরেছে?
মতলুব আলী : আমাদের দীর্ঘদিনের ইতিহাস বলে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেছে, তারা প্রাইজ পেয়েছে। আন্তর্জাতিক মান যেটা বলছ, সেটা তারা পূরণ করেছে। এখানে একটা প্রশ্ন আছে, আমাদের যারা সক্রিয় শিল্পী তাদের মৌলিক কনট্রিবিউশন থাকতে হবে। যেটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের থেকে অন্য দেশের শিল্পীরা প্রভাবিত হবেন। সেটা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়নি এখনো। আমরা গ্রহণ করি। বাইরে থেকে প্রভাবিত হই, তারপর অংশগ্রহণ করি। আমাদের নিজস্বতা তৈরি করতে হবে।
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : জাকির উসমান ও নুসরাত নুসিন